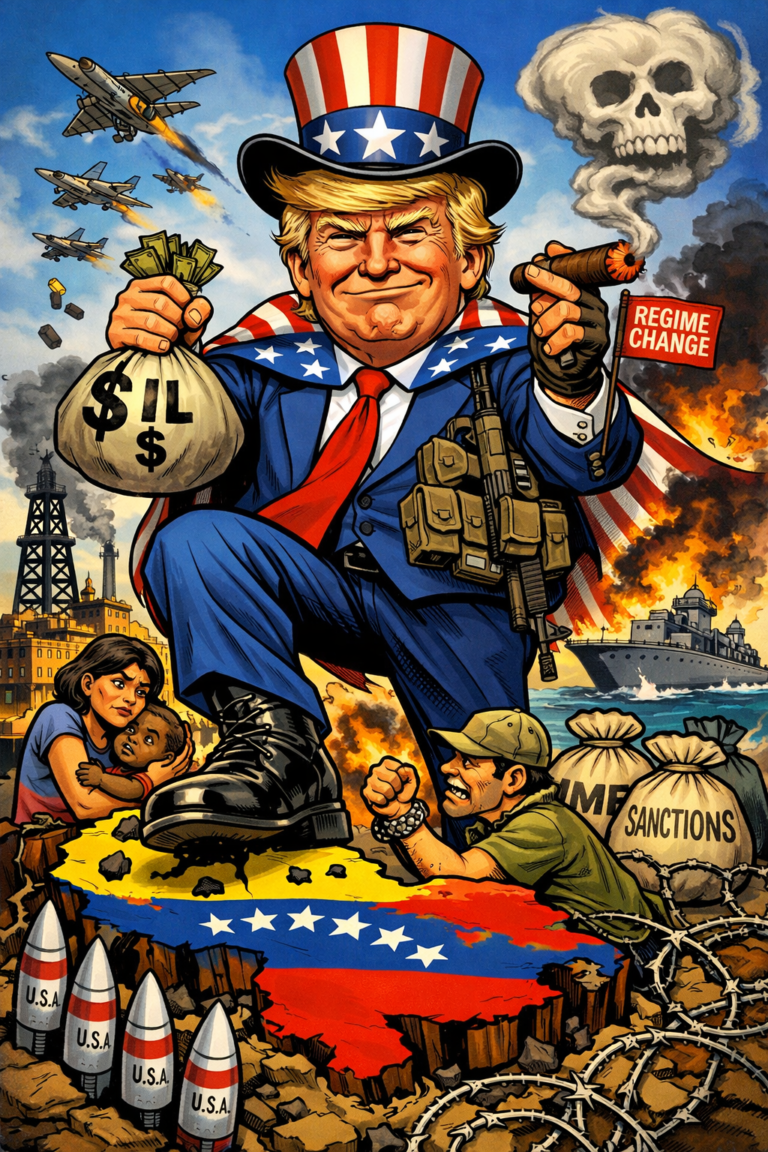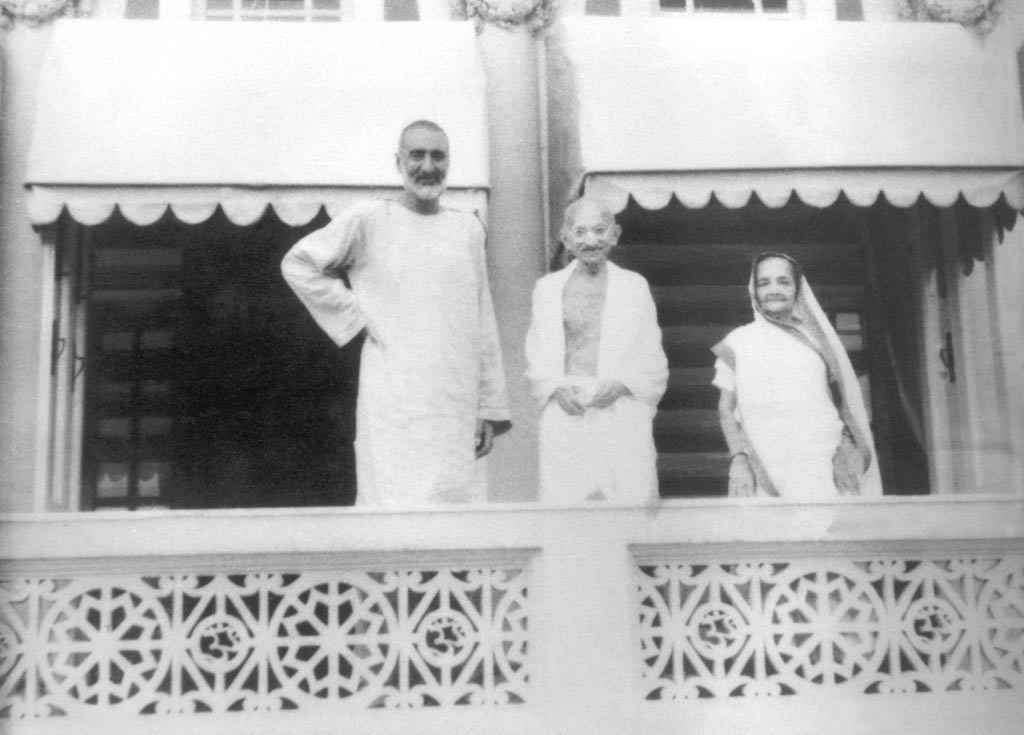
পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস (পিএনসি) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (আইএনসি)-এর উত্তরসূরি ছিল, একথা খুব কম লোকই জানে। পিএনসি শুধু ১৯৪৭-এর পর প্রথম অফিশিয়াল বিরোধী দলই ছিল না, এটি কেন্দ্রে এবং পূর্ব পাকিস্তানে (এখনকার বাংলাদেশ) কোয়ালিশন পার্টনার হিসেবে ক্ষমতাও ভাগ করে নিয়েছিল।
ব্রিটিশ ভারতের ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের ৬৯ সদস্যের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (আইএনসি)-এর প্ল্যাটফর্ম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ১২ জন সদস্য এই অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়েছিল। আইএনসি-র উত্তরসূরি পিএনসি-এর পূর্ব পাকিস্তান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতেও প্রতিনিধি ছিল। পিএনসি-র সদস্যরা বিরোধী দল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে এবং দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে নেওয়া অন্যান্য আইনি প্রচেষ্টার বিরোধিতায়। পিএনসি একটা গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলত এবং অহিংসার প্রচার করত। কিন্তু মূলধারার ইতিহাসের লেখাপত্র আর শিক্ষার পাঠ্যবইয়ে পিএনসি-র কথা প্রায় বাদই দেওয়া হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, ক্রমশ ইসলামিকরণ হওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পিএনসি-র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।
ফারুক সুলেহরিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ড. তাহির কামরান ইতিহাস ও রাজনীতির মূলধারার আলোচনায় পিএনসি-র অস্তিত্ব বিষয়ে সার্বিক নীরবতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। ড. কামরান পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদ, একাডেমিক এবং পাবলিক বুদ্ধিজীবীদের একজন। তিনি পাকিস্তানের ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রকাশনা করেছেন। তার সাম্প্রতিক বই হলো চেকার্ড পাস্ট, আনসার্টেন ফিউচার: দ্য হিস্ট্রি অফ পাকিস্তান (২০২৪)।
পিএনসি, আইএনসি–র উত্তরসূরি হিসেবে, পাকিস্তানের প্রথম সংসদ কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে প্রথম অফিশিয়াল বিরোধী দল গঠন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসের বইয়ে, মূলধারার বা অন্যথায়, পিএনসি–র কোনো উল্লেখ নেই। পিএনসি–র এই সার্বিক অনুপস্থিতির কারণ কী?
তাহির কামরান: পাকিস্তানের ইতিহাসের বইয়ে পিএনসির উল্লেখ কোত্থাও না থাকার সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় দেশের শুরু থেকেই গড়ে ওঠা কট্টর রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। পাকিস্তানের প্রাথমিক রাজনৈতিক কাঠামো মতপার্থক্য বা ভিন্নমতের জন্য খুব কম বা প্রায় কোনো জায়গাই রাখেনি। মুসলিম লীগ, রাষ্ট্রের প্রধান দল এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, একটা প্রায় একদলীয় শাসনের কল্পনা করেছিল, যেখানে বিকল্প রাজনৈতিক আখ্যান—বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত, যা ছিল তাদের আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বী—অগ্রহণযোগ্য ছিল।
পিএনসি আইএনসি-র উত্তরসূরি হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে একটা রাজনৈতিক এবং আবেগপ্রবণ উত্তরাধিকার পেয়েছিল। লোকে পিএনসি-কে একটা বৈধ বিরোধী দল হিসেবে দেখেনি, বরং দেশভাগের আগের শত্রুর অবশিষ্টাংশ হিসেবে গণ্য করেছিল। এই ধারণা মুসলিম লীগ এবং তার নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কাছে পিএনসি-কে রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।
এই অগ্রহণযোগ্যতা ১৯৪৯ সালে অবজেক্টিভস রেজোলিউশন (যেটা ১৯৫৬ এবং ১৯৭৩ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনা হয়ে উঠেছে) নিয়ে বিতর্কের সময় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। পিএনসি, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব ক’রে এবং একটা ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বজনীন পাকিস্তানের পক্ষে কথা ব’লে, রেজোলিউশনের স্পষ্ট ইসলামিক প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তাদের আপত্তি আলোচনার মাধ্যমে নয়, বরং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের যুক্তিকে যুক্তি দিয়েই বিবেচনার বদলে, শাসক শ্রেণি তাদের উড়িয়ে দিয়েছিল, যা রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে মেনে নিতে বৃহত্তর অনীহার প্রতিফলন করে।
এমন পরিবেশে, পিএনসি-কে জাতীয় আখ্যান থেকে পদ্ধতিগতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল, এটা আশ্চর্যের নয়। পাকিস্তানের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে প্রথম অফিশিয়াল বিরোধী দল হিসেবে এর ভূমিকা মূলধারার ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, এর গুরুত্বের অভাবে নয়, বরং ঠিক এই কারণে যে এর উপস্থিতি মুসলিম লীগের অধীনে একটি এককেন্দ্রিক মুসলিম রাজনৈতিক প্রকল্পের প্রধান আদর্শগত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। পিএনসি-র প্রান্তিকিকরণ তাই প্রমাণ করে যে প্রাথমিক পাকিস্তানি রাজনীতি কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে ভিন্নমতকে প্রাতিষ্ঠানিক করা-কে এড়িয়ে গেছে এবং রাষ্ট্রের জন্য বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গিকে দমন করেছে।
সমাজ বিজ্ঞান এবং পাকিস্তান স্টাডিজের পাঠ্যবইয়ে পিএনসি–র কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। কেন?
তাহির: এ. এইচ. নাইয়ার এবং আহমেদ সালিম তাদের দ্য সাট্ল সাবভার্সন-এ যুক্তি দিয়েছেন যে, পাকিস্তান শুরু থেকেই বর্জনের পথ অনুসরণ করেছে, জাতীয় আখ্যানে বহুত্ববাদ বা সর্বজনীনতার জন্য কোনো জায়গা পদ্ধতিগতভাবে বাদ দিয়েছে। এই ইচ্ছাকৃত বর্জন একটি একক, রাষ্ট্র-চালিত আদর্শের মধ্যে নিহিত ছিল, যা পাকিস্তানকে একটি এককেন্দ্রিক ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করিয়েছিল, যা প্রায়শই ভারতের সঙ্গে সরাসরি বিরোধিতায় ছিল, যাকে পাকিস্তানি শাসক শ্রেণি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করেছিল। পাকিস্তানের আদর্শগত জায়গার মূল ভিত্তি ছিল ভারতের প্রতি ভয় এবং শত্রুতা, যা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বিরোধী দলের সঙ্গে আচরণে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।
এই কাঠামোর মধ্যে, পিএনসি-কে—যদিও তা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে প্রথম অফিশিয়াল বিরোধী দল ছিল—শুধু প্রান্তিকই করা হয়নি, বরং জাতীয় স্মৃতি থেকে সক্রিয়ভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান এবং পাকিস্তান স্টাডিজের পাঠ্যবইয়ে পিএনসি-র উপস্থিতি এবং অবদান সম্পূর্ণ মুছে ফেলা বিশেষভাবে স্পষ্ট। এর কারণ আদর্শগত এবং রাজনৈতিক উভয়ই।
পিএনসি, আইএনসি-র উত্তরসূরি হিসেবে, ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ এবং একটি অংশভাক ভারতীয়-মুসলিম ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার প্রতীক ছিল—এমন মূল্যবোধ যা পাকিস্তানের জন্য তৈরি করা একচেটিয়া ইসলামিক পরিচয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। ভারতের সঙ্গে এর যোগসূত্র, সঙ্গে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব, এটিকে শাসক আখ্যানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছিল। পাঠ্যবইয়ে পিএনসি-কে স্বীকার করা মানে হতো এটা স্বীকার করা যে প্রাথমিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে, যতই সীমিত হোক না কেন, ভিন্নমত, ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং সংখ্যালঘু কণ্ঠের জন্য জায়গা ছিল—এমন একটা স্বীকৃতি যা শাসক শ্রেণি দিতে অনিচ্ছুক ছিল।
তাই, পাঠ্যবই থেকে পিএনসি-র সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করে: প্রথমত এই ধারণাকে জোরদার করে যে পাকিস্তান শুরু থেকেই আদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল, এবং তা ভারতের সঙ্গে চিরস্থায়ী আদর্শগত বিরোধিতার আখ্যান বজায় রাখে। এটা করতে গিয়ে ইতিহাসের স্মৃতিকে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা সমর্থন করতে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দমন করার মতো করে গঠন করা হয়েছে। পিএনসি-র অদৃশ্যকরণ কোনো ঐতিহাসিক ভুল নয়; এটা একটা সচেতন আদর্শগত প্রকৌশলের কাজ।
আপনি ২০২৪ সালে চেকার্ড পাস্ট, আনসার্টেন ফিউচার: দ্য হিস্ট্রি অফ পাকিস্তান নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। যদিও এটি পিএনসি–র নেতা এবং সংসদ সদস্য যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডলের উল্লেখ করে, বইটি পিএনসি–কে একটি বিষয় হিসেবে আলোচনা করে না। এই বাদ দেওয়া কি স্ব–সেন্সরশিপ, বাইরের সেন্সরশিপ, নাকি পাকিস্তানি ইতিহাসবিদদের পিএনসি–কে অপ্রাসঙ্গিক মনে করার ফল?
তাহির: আমার বই চেকার্ড পাস্ট, আনসার্টেন ফিউচার: দ্য হিস্ট্রি অফ পাকিস্তান (২০২৪)-এ পিএনসি-র বিস্তারিত আলোচনার অনুপস্থিতি স্ব-সেন্সরশিপ বা বাইরের সেন্সরশিপের ফল নয়। বরং, এটা অজ্ঞানে বাদ দেওয়া এবং দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তানি ইতিহাসবিদদের ঐতিহাসিক অবহেলার একটা প্রতিফলনের সমন্বয়।
বইটির বিস্তৃত পরিধি, যা পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংবিধানিক বিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে, তার কঠিন সম্পাদনার সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। স্থানের সীমাবদ্ধতা এবং বিষয়গত সীমাবদ্ধতার কারণে, কিছু দিক যতটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ততটা গভীরভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো ব্যক্তিত্ব পিএনসি-র উল্লেখ করলেও, এটি দুর্ভাগ্যবশত উপেক্ষিত বিষয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। আমি এটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিনি; তবে, পাকিস্তানের প্রচলিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এটাকে দীর্ঘদিন ধরে তেমনই মনে করে এসেছে।
মূলধারার ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে পিএনসি-কে মুছে ফেলা পাকিস্তানের জাতীয় আখ্যানের মধ্যে একটা বৃহত্তর সমস্যা প্রতিফলিত করে। নাইয়ার এবং সালিম দ্য সাবটল সাবভার্সন-এ যেমন উল্লেখ করেছেন, এই আখ্যানটি একটি বর্জনের যুক্তি দ্বারা গঠিত হয়েছে যা বহুত্ববাদকে দমন করে এবং ভিন্নমতকে প্রান্তিক করে। পিএনসি, যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত এবং প্রায়শই রাষ্ট্রের আদর্শগত দিকনির্দেশনা থেকে ভিন্ন মত পোষণ করত, তাদের পাঠ্যবই, আর্কাইভ এবং শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগত স্মৃতি থেকে নিঃশব্দে বাদ দেওয়া হয়েছে।
আমার কাজে এই বাদ দেওয়া যদিও সেই প্রবণতার ধারাবাহিকতা বলে মনে হতে পারে, তবে এটা ইচ্ছাকৃত দমনের কাজ ছিল না। তবুও, এটা পাকিস্তানি ইতিহাসবিদদের—আমাকে ধরেই বলছি—ঐতিহাসিক আখ্যানে আমাদের অগ্রাধিকারগুলো সমালোচনামূলকভাবে পুনর্মূল্যায়ন করার এবং পিএনসি-র মতো কণ্ঠ এবং প্রতিষ্ঠানকে জায়গা দেওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যারা প্রচলিত গল্পকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের প্রান্তিকিকরণ স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না; এটা সংগঠিত হয়েছিল, এবং এখন সময় এসেছে আমাদের সেই নীরবতাকে ভাঙতে শুরু করবার।
আপনি কি মনে করেন পিএনসি–র উপর গবেষণা করা, আলোচনা করা এবং পাঠ্যবইয়ে এবং উচ্চশিক্ষার ইতিহাস মডিউলে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কেন?
তাহির: হ্যাঁ, অবশ্যই—পিএনসি-র উপর গবেষণা করা, আলোচনা করা এবং পাঠ্যবইয়ে এবং উচ্চশিক্ষার ইতিহাস মডিউলে এটিকে অর্থপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পিএনসি-র অন্তর্ভুক্তি শুধু ঐতিহাসিক পূর্ণতার বিষয় নয়; এটা একটা গণতান্ত্রিক অপরিহার্যতা।
মতের বহুত্ব এবং প্রতিযোগী আখ্যান যে কোনো সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যারা গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে জড়িত হতে চায়। পাকিস্তানের প্রাথমিক রাজনৈতিক দৃশ্যপট বেশিরভাগ পাঠ্যবইয়ে উপস্থাপিত একক আখ্যানের তুলনায় অনেক বেশি জটিল এবং বিতর্কিত ছিল। পিএনসি, কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে প্রথম অফিশিয়াল বিরোধী দল এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কণ্ঠ হিসেবে, পাকিস্তানের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল যা সর্বজনীনতা, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন এবং সাংবিধানিকতার উপর জোর দিয়েছিল। সেই কণ্ঠকে উপেক্ষা করা পাকিস্তানের রাজনৈতিক শুরুর বোঝাপড়াকে বিকৃত করে।
পিএনসি-র অধ্যয়নের মাধ্যমে, ছাত্র এবং পণ্ডিতরা পাকিস্তানের পরিচয় গঠনের বিতর্কিত প্রকৃতিকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এটা ইতিহাসের এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহায্য করে এবং দেশের গঠনমূলক বছরগুলোতে করা বিবেচনাগুলোর উপর সমালোচনামূলক প্রতিফলনের জন্য জায়গা খুলে দেয়। এটা শুধু ঐতিহাসিক নির্ভুলতার জন্যই নয়, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলার জন্যও অপরিহার্য।
একাডেমিক আলোচনায় পিএনসি-র অন্তর্ভুক্তি তাদের দৃশ্যমানতা পুনরুদ্ধার করবে যারা পদ্ধতিগতভাবে প্রান্তিক হয়েছিল—শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, ঐতিহাসিক রেকর্ডেও। এটা পাকিস্তানের বহুত্ববাদী অতীতকে স্বীকার করার প্রতিশ্রুতিকে নির্দিষ্ট করবে এবং, এর ফলে, আরও সর্বজনীন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।
পাকিস্তানের ইতিহাসে আর কোন কোন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রকল্প অদৃশ্য, মুছে ফেলা বা প্রান্তিক করা হয়েছে?
তাহির: পাকিস্তানে অতীতের অনেক ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রকল্প পদ্ধতিগতভাবে অদৃশ্য, মুছে ফেলা বা প্রান্তিক করা হয়েছে—প্রাথমিকভাবে কারণ তারা প্রধান রাষ্ট্রীয় আখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। প্রান্তিক কণ্ঠগুলো, বিশেষ করে যারা বামপন্থী, জাতিগতভাবে ভিন্ন বা আদর্শগতভাবে বহুত্ববাদী ছিল, পাকিস্তানের জাতীয় আলোচনায় কখনো অর্থপূর্ণ স্থান পায়নি। এই মুছে ফেলা ইতিহাসের শিক্ষা, স্মৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিকিকরণে একটা বিপজ্জনক এককেন্দ্রিকতা তৈরি করেছে।
পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস (পিএনসি) ছাড়াও, আরও বেশ কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন এবং উদ্যোগ একই দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে:
কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী আন্দোলন: পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিপি), মজদুর কিসান পার্টি এবং পরে ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (এনএপি)-এর মতো বামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা হয় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বা তাদের দুর্নাম ছড়ানো হয়েছে। শ্রমিক অধিকার আলোচনা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও, তারা পাঠ্যবই এবং জনসাধারণের স্মৃতি থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন থেকে গেছে।
ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (এনএপি): এই জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক দল বালোচ, পশতুন, সিন্ধি এবং বাঙালি জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭৫ সালে এটি নিষিদ্ধ করা হয়, এবং এর নেতাদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়—এটা আরও প্রমাণ করে যে রাষ্ট্র কীভাবে জাতিগত বহুত্ব এবং বামপন্থী রাজনীতিকে দমন করেছে।
বাঙালি স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন: ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠন করলেও, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা মূলধারার আখ্যানে খুব কমই ন্যায্যতা বা গভীরতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা এবং বাংলাদেশ গঠনের পুরো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রায়শই “ভারতীয় ষড়যন্ত্র” নামক অতি সরলীকৃত ধারণায় পর্যবসিত করা হয়, কাঠামোগত অসমতা এবং রাজনৈতিক দমনকে উপেক্ষা করে।
সিন্ধি এবং বালোচ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: বৃহত্তর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ফেডারেল অতিক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষে আন্দোলন—যেমন সিন্ধি জিয়ে সিন্ধ আন্দোলন এবং বিভিন্ন বালোচ জাতীয়তাবাদী প্রকল্প—হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী হুমকি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে বা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে, যদিও তাদের শিকড় গণতান্ত্রিক দাবি এবং সাংবিধানিক ফেডারেলিজমে।
নারী এবং সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলন: নারীদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন, বিশেষ করে জেনারেল জিয়া-উল-হকের শাসনামলে (যেমন, উইমেন্স অ্যাকশন ফোরাম), এবং সমান নাগরিকত্বের জন্য লড়াই করা ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, আনুষ্ঠানিক ঐতিহাসিক আখ্যানের প্রান্তে রয়ে গেছে।
এই নির্বাচনী স্মৃতি, আদর্শগত সম্মতি এবং অভ্যন্তরীণ বহুত্বের ভয় দ্বারা চালিত, পাকিস্তানের ইতিহাসের একটা বিপজ্জনকভাবে একপেশে বোঝাপড়া তৈরি করেছে। এই বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক প্রকল্পগুলোকে উপেক্ষা করে, রাষ্ট্র শুধু অগণিত সম্প্রদায়ের সংগ্রাম মুছেই ফেলেনি, বরং একটি আরও সর্বজনীন এবং গণতান্ত্রিক সমাজে বেড়ে ওঠার সুযোগও নিজে অস্বীকার করেছে। এই আখ্যানগুলো পুনরুদ্ধার করা আরও সৎ এবং সমন্বিত জাতীয় পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য।
বঙ্গানুবাদঃ সিদ্ধার্থ বসু